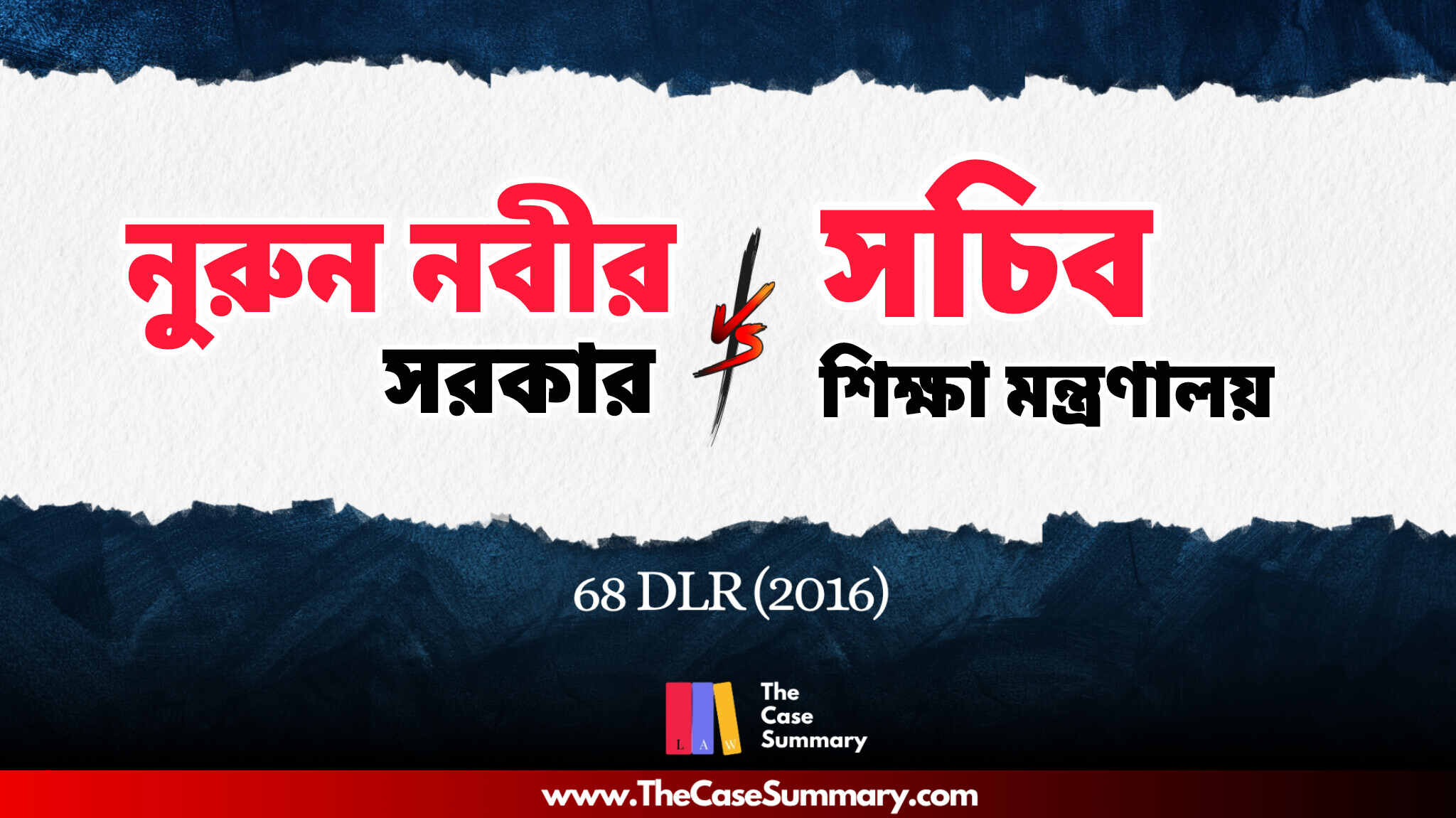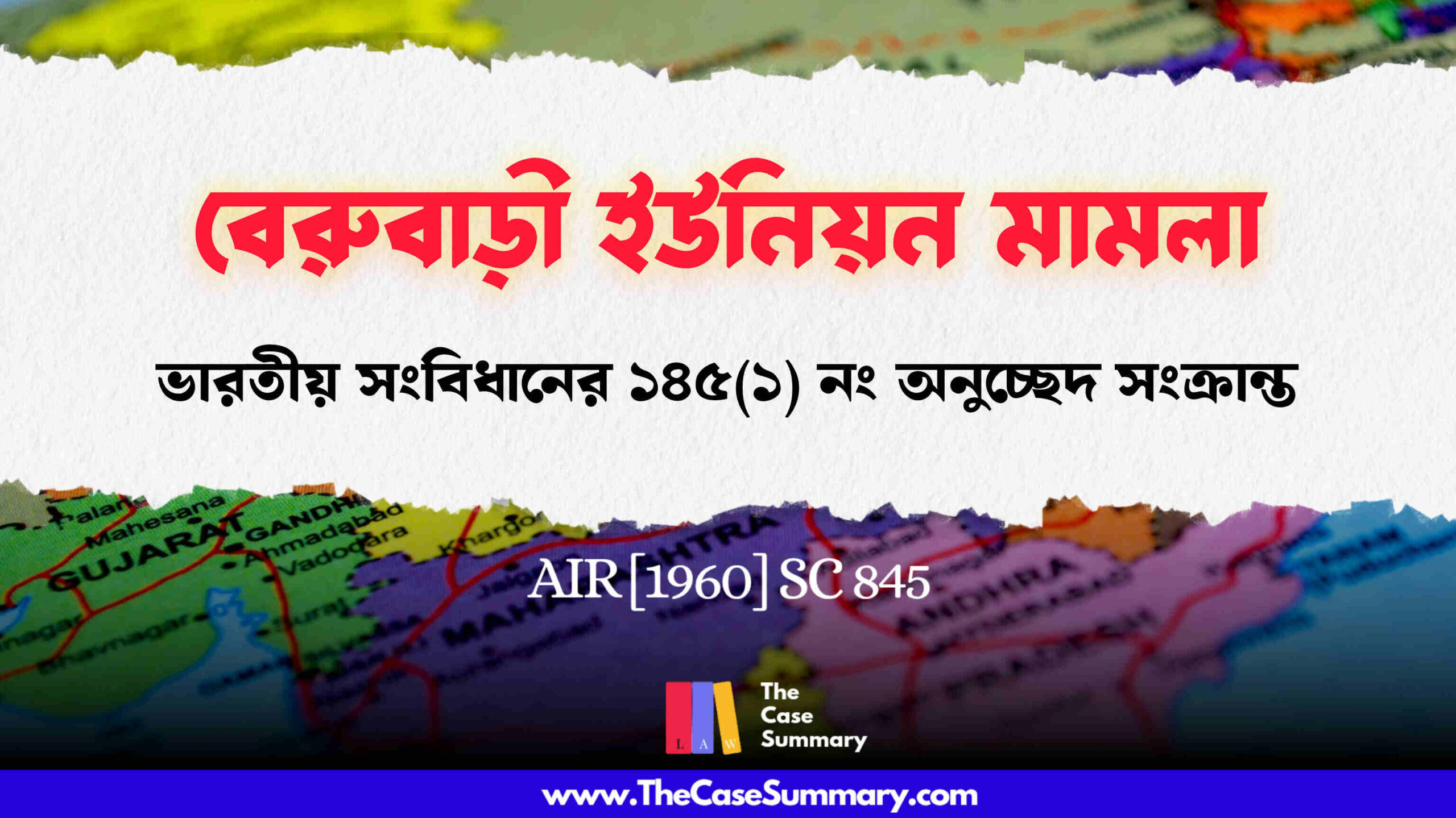ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ
‘সেকশন ৫৪ গাইডলাইন্স কেইস‘ বা ‘রুবেল হত্যা মামলা‘ বা ‘গাইডলাইন্স অন অ্যারেস্ট এন্ড রিমান্ড কেইস‘
সাইটেশন : 55 DLR (2003) 363
জুরিসডিকশন : বাংলাদেশ
আবেদনকারী : বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন ও শালিশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন এবং অন্যান্য
বিবাদী : বাংলাদেশ ও অন্যান্য
পটভূমি :
বাংলাদেশের মানুষ বছরের পর বছর ধরে দেখেছে, সাধারণ নাগরিকদের কোন প্রকার ব্যাখ্যা ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, এবং কখনও কখনও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তি আর [পরিবারের নিকট] ফিরে আসে না। এই গ্রেপ্তারগুলি ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (CrPC) এর ধারা ৫৪ এর অধীনে করা হতো, যেখানে পুলিশকে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে ওয়ারেন্ট ছাড়াই কাউকে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। তদুপরি, ধারা ১৬৭ এর অধীনে অনেককে পুলিশ রিমান্ডে নেওয়া হতো, যা প্রায়শই নির্মম নির্যাতন মাধ্যমে শেষ হতো। এরকম একজন ভুক্তভোগী ছিলেন রুবেল, যাকে ধারা ৫৪ এর অধীনে কোন প্রকার আনুষ্ঠানিক অভিযোগ ছাড়াই গ্রেপ্তার করা হয়, এবং কয়েক দিন পর তার মৃতদেহ পরিবারের কাছে ফেরত দেওয়া হয়। এটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, যেমন ২০০২ সালে মাত্র এক বছরে অন্তত ৩৮টি হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছিল।
ঘটনা :
বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট), আইন ও সালিশ কেন্দ্র, সম্মিলিত সামাজিক আন্দোলন এবং অন্যান্য ব্যক্তিগণ বাংলাদেশ সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীনে রিট পিটিশন দায়ের করেন (রিট পিটিশন নং ১৯৯৮ এর ৩৮০৬)। আবেদনকারীগণ ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর ধারা ৫৪ এবং ১৬৭ এর অধীনে পুলিশের ক্ষমতার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানান। তারা যুক্তি উত্থাপন করেন যে, উক্ত বিধানগুলি অপব্যবহার করা হচ্ছিল, যা প্রায়শই পুলিশি হেফাজতে নির্যাতন এবং মৃত্যুর মতো ঘটনার দিকে নিয়ে যায়। তারা দাবি করেন, এরূপ কার্যক্রম সংবিধানের অনুচ্ছেদ ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৫ এর অধীনে মৌলিক অধিকার লঙ্ঘন শামিল। আবেদনকারীগণ আরও উল্লেখ করেন, পুলিশ প্রায়ই সকল প্রকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা উপেক্ষা করে, বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪ এর ধারা ৩ এর অধীনে প্রতিরোধমূলক আটক করার অজুহাত হিসেবে ধারা ৫৪ কে ব্যবহার করত। তারা রুবেল হত্যাসহ বেশ কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করেন।
ইস্যু :
১. ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮-এর ৫৪ ধারার অধীনে গ্রেপ্তার করার ক্ষমতা কি সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৫ অনুচ্ছেদের সাথে সাংঘর্ষিক?
২. বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর ধারা ৩-এর অধীনে প্রতিরোধমূলক আটক করার উদ্দেশ্যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৪ ব্যবহার করা কি আইনসম্মত?
৩. ফৌজদারি কার্যবিধির ১৬৭ ধারার অধীনে রিমান্ড মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কি ম্যাজিস্ট্রেটগণের বিচারিক বিবেচনা প্রয়োগের বাধ্যবাধকতা রয়েছে?
৪. অবৈধ গ্রেপ্তার, আটক এবং হেফাজতে নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিরা কি ক্ষতিপূরণের অধিকারী?
সিদ্ধান্ত :
সম্পূর্ণ শুনানি শেষে হাইকোর্ট ২০০৩ সালের ৭ এপ্রিল রায় প্রদান করেন, যেখানে উল্লেখ করা হয় যে, ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৪ এবং ১৬৭ সম্পূর্ণভাবে সাংবিধানিক নয়, কারণ এগুলি সংবিধানের ২৭, ৩১, ৩২, ৩৩ এবং ৩৫ অনুচ্ছেদের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। আদালত একটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করেন, যার মধ্যে ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৫৪ এবং ১৬৭ সংশোধন করার বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল, এবং উক্ত সংশোধনী ছয় মাসের মধ্যে বাস্তবায়নের নির্দেশ প্রদান করেন। এছাড়াও, আদালত রায় প্রদান করেন যে, এসব ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী। উপরন্তু, হাইকোর্ট নিম্নলিখিত ১৫টি নির্দেশনা জারি করেন:
১. পুলিশ শুধু বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪-এর অধীনে আটক করার উদ্দেশ্যে ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারায় কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারবে না।
২. গ্রেপ্তার করার সময় যদি পরিচয় জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহলে পুলিশকে তাদের পরিচয়পত্র দেখাতে হবে এবং নিজেদের পরিচয় দিতে হবে।
৩. একটি বিশেষ রেকর্ড চালু না হওয়া পর্যন্ত পুলিশকে গ্রেপ্তারের কারণ এবং অন্যান্য বিবরণ একটি রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
৪. যদি গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তির শরীরে আঘাতের চিহ্ন থাকে, তবে পুলিশকে তার কারণ লিখতে হবে এবং তাকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে বা সরকারি চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যেতে হবে ও চিকিৎসা সনদ সংগ্রহ করতে হবে।
৫. গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে পুলিশ স্টেশনে আনার তিন ঘণ্টার মধ্যে গ্রেপ্তারের কারণ জানাতে হবে।
৬. যদি কোন ব্যক্তিকে তার বাড়ি বা কর্মস্থলের বাইরে থেকে আটক করা হয়, তবে পুলিশকে এক ঘণ্টার মধ্যে তার পরিবারের সঙ্গে ফোন বা বার্তাবাহকের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে হবে।
৭. গ্রেপ্তারকৃত ব্যক্তিকে তার ইচ্ছা অনুযায়ী একজন আইনজীবী বা ঘনিষ্ঠ পরিবারের সদস্যের সাথে কথা বলার অনুমতি দিতে হবে।
৮. অভিযুক্তকে আদালতে উপস্থাপনের সময় পুলিশকে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করতে হবে:
• কেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি?
• কেন গ্রেপ্তারকে ন্যায়সংগত বলে মনে করা হয়েছে?
• মামলার নথিপত্রের অনুলিপি ম্যাজিস্ট্রেটকে সরবরাহ করতে হবে।
৯. যদি ম্যাজিস্ট্রেট মনে করেন যে গ্রেপ্তার ন্যায়সংগত, তবে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে রাখার আদেশ দিতে পারেন। অন্যথায়, তাকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে।
১০. যদি ম্যাজিস্ট্রেট দেখেন যে, গ্রেপ্তার অন্যায়ভাবে এবং যথাযথ প্রমাণ ছাড়া করা হয়েছে, তবে দণ্ডবিধির ২২০ ধারার অধীনে গ্রেপ্তারকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অন্যায়ভাবে আটক রাখার অপরাধে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে।
১১. যদি ম্যাজিস্ট্রেট জেলে আটক রাখার নির্দেশ প্রদান করেন, তবে একটি বিশেষ জিজ্ঞাসাবাদ কক্ষ প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনীয় জিজ্ঞাসাবাদ জেলের ভিতরেই করতে হবে।
১২. জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজত চাওয়ার সময় তদন্ত কর্মকর্তাকে স্পষ্টভাবে কারণ উল্লেখ করতে হবে।
১৩. যদি ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ হেফাজত মঞ্জুর করেন, তাহলে তাকে আটক ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষিত করতে নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করতে হবে।
১৪. যদি পুলিশ বা জেল হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হয়, পুলিশ বা জেল কর্তৃপক্ষকে অবিলম্বে তা নিকটস্থ ম্যাজিস্ট্রেটকে জানাতে হবে।
১৫. হেফাজতে মৃত্যুর তথ্য পাওয়ার সাথে সাথে ম্যাজিস্ট্রেটকে তদন্ত শুরু করতে হবে।
সংশ্লিষ্ট আইন :
- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
- অনুচ্ছেদ : ২৭, ৩২, ৩২, ৩৩, ৩৫, ১০২
- ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮
- ধারা : ৫৪, ১৬৭
- বিশেষ ক্ষমতা আইন, ১৯৭৪
- ধারা : ৩
অনুবাদক :
১. মো. আতিকুর রহমান
[সতর্কতা : উক্ত মামলার বাংলা সংস্করণটি মূল ইংরেজি হতে অনূদিত। অর্থগত সামঞ্জস্যতা বজায় রাখার সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা করা হয়েছে। কোনো প্রকার অসামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হলে, মূল ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে।]
নোট : The Case Summary আইনের শিক্ষার্থীদের জন্য এবং আইনের শিক্ষার্থীদের দ্বারা তৈরি একটি প্ল্যাটফর্ম। আমরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে নির্ভুলভাবে বাংলা ও ইংরেজি উভয় ভাষায় বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার ঘটনা ও রায় তুলে ধরার চেষ্টা করি। এই প্ল্যাটফর্মটি কখনোই পূর্ণাঙ্গ আইনের ধারণা প্রদান করে না, আমরা শিক্ষার্থীদের শুধু মাত্র মামলার সারাংশ নির্ভর হওয়াকে নিরুৎসাহিত করি। ধন্যবাদ